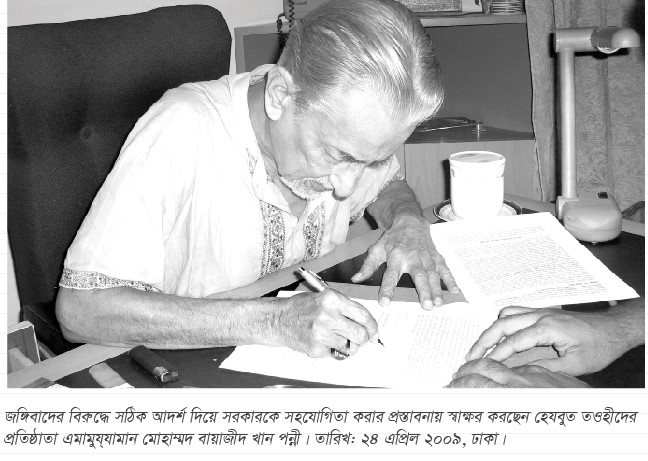রিয়াদুল হাসান:
শেষ রসুলের (সা.) মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা মানবজাতির একটি অংশে প্রয়োগ ও কার্যকর করার ফল কী হয়েছিল তা একবার দেখা যাক। যারা আমার এই লেখা পড়ছেন, তাদের অনুরোধ করছি আপনারা মনে মনে কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সমাজ কল্পনা করুন। কল্পনা করুন এই সমাজে অস্ত্র কিনতে বা তৈরি করতে কোনো বাধা নেই, কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন পড়ে না, যে কেউ অস্ত্র কিনে বা তৈরি করে তার ঘর ভরে ফেললেও কেউ তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। কল্পনা করুন, এই সমাজে কোনো আইন শৃংখলা রক্ষাকারী অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী নেই। বর্তমানের মতো হাজার হাজার লোক রাখার উপযোগী কোনো জেলখানাও সেখানে নেই। শুধু বড় বড় শহরগুলিতে দুই চারজন লোক রাখার মতো ছোট জেলখানা আছে। কিন্তু সমাজে বলতে গেলে কোনো অপরাধ নেই। বিচারালয়গুলিতে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা প্রায় অনুপস্থিত।
আমি জানি, এমন একটি সমাজ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমার আরজ হচ্ছে, আপনারা যা কল্পনা করতে পারছেন না, তা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের জাতি গঠন থেকে শুরু করে এই জাতির আদর্শচ্যুতির ফলে পতন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত বহু বছর ধরে এই অবস্থা বিরাজ করেছিল। অস্ত্রের মালিকানা, অস্ত্র তৈরি ও বিক্রয়ের উপর সামান্যতম কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও, দেশে কোনো পুলিশবাহিনীর উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। দুই একটি অপরাধের ঘটনা কালেভদ্রে ঘটলেও অপরাধী নিজে এসে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দাবি করত। তাকে ধরে আনারও প্রয়োজন পড়ত না। এই অকল্পনীয় অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? এর একমাত্র কারণ, মানুষ মানবরচিত সকল ব্যবস্থা, বিধান প্রত্যাখ্যান করে তার স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিল অর্থাৎ ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান মানবো না’ এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করেছিল। আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোনো কিছু ঘটতে দেখলে সেটা ঐ সমাজের কেউ বরদাস্ত করত না, সবাই সমস্বরে সেটার প্রতিবাদ জানাতো। বর্তমান সময়ে যেমন অন্যায় করেও মানুষ সমাজে সম্মানের আসন পায়, ইসলামপূর্ব আরবের জাহেলিয়াতের যুগেও সেটা হত। ইসলাম মানুষকে এখান থেকে সরিয়ে তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমাজের প্রতিটি মানুষ সেই মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। ফলে সেই সমাজে থেকে কেউ কোনো অন্যায় করলে সে সমাজের আশ্রয় হারাতো, নিজ সমাজে সে ধিকৃত ও নিন্দিত হত, সামাজিক মর্যাদা হারাতো। এই কারণে মানুষ অন্যায় করতে নিরুৎসাহিত হত। পাশাপাশি ছিল কঠোর আইনের শাসন। এসব মিলিয়ে অপরাধ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। রসুলাল্লাহর যুগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তার জন্য কোনো পুলিশ বাহিনীরও প্রয়োজন হয়নি। কারণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান করার দায়িত্ব প্রত্যেক মো’মেনের আর মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে তাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। (সুরা ইমরান ৩:১১০)। আল্লাহ আরো বলেছেন, ‘তোমরা উত্তম কাজে ও আল্লাহর মানদণ্ড রক্ষায় সাহায্য করো এবং পাপকর্ম ও পরস্পরকে সীমালংঘনের কাজে সাহায্য করো না।’ (সুরা মায়েদা ৫:২)
তবে পরবর্তীতে খলিফা উমরের (রা.) সময় ইসলামিক রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির পর নিয়মিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয় যার নাম ছিল ‘আশ-শুরতা’। নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধ দমন করা, অপরাধীদের গ্রেফতার করা, আদালতের রায় মোতাবেক শাস্তি কার্যকর করা, বাজারের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সরকারি সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো রক্ষা করা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বা বিদ্রোহীদের সনাক্ত করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা যে কোনো বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল এই বাহিনীর কাজ। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে আশ-শুরতার প্রধানকে সাহিব আশ-শুরতা (Head of National Security) বলা হতো।
মধ্যযুগের অর্থাৎ সুলতানি যুগের পুলিশি কার্যক্রমের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, রাষ্ট্র শুধু অপরাধীদেরকেই আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিত না, প্রয়োজনে চুরি-ডাকাতির ক্ষেত্রে কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্য এবং অপরাধীদেরকে ধরতে না পারার ব্যর্থতায় ক্ষতিগ্রস্তকে পুষিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাসহ দায়ীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করত। এমনকি এই দায়ীদের তালিকায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরও রেহাই দেওয়া হতো না। (History of the Rise of the Mahomedan Power in India of Mahomed Kasim Ferishta)।
আমাদের বাংলাদেশে আফগান সুলতান শেরশাহের আমলে গ্রামে চুরি, ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় গ্রাম-প্রধানকেই প্রথমে এই মর্মে দায়ী করা হতো যে, হয় সে অপরাধীকে সশরীরে ধরে এনে আইনের হাতে সোপর্দ করবে, না হলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে। অপরাধীকে যে কোনোভাবে ধরে এনে ন্যায়বিচারান্তে কঠোর শাস্তিপ্রদান অথবা সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে বিকল্প হিসেবে দায়িত্ববান কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের বাধ্যতামূলক নিয়ম প্রবর্তনের একটি অনিবার্য ও ইতিবাচক ফল এই হয়েছিল, সুলতানিযুগে বিশেষত শেরশাহের সময়ে সাম্রাজ্যব্যাপী আইন-শৃঙ্খলার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তারিখ-ই-ফিরিশতার সূত্রে জানা যায়: বাংলা, সোনারগাঁও থেকে শুরু করে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল দূরত্বের পথে এতটাই নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, শেরশাহ সুরির শাসনামলে পথচারী ও বণিকদের অনেকেই রাস্তার পাশে তাদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রি রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। তাদের মনে ডাকাতির হওয়ার কোনো ভয় জাগত না। ইংরেজ ঐতিহাসিক হেনরি বেভারেজ বলেছেন, বাংলা থেকে কাবুল, তেলেঙ্গানা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পথিক ও বণিকরা তাদের মালপত্র রেখে রাজপথে নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। (অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস- কাবেদুল ইসলাম)। কোরায়েশদের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার সাহাবিদেরকে আশ্বস্ত করতে আল্লাহর রসুল ভবিষ্যতের এই পরিস্থিতির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সময় আসছে যখন একা একটি যুবতী নারী মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দিনে ও রাতে সা’না থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে, তার মনে এক আল্লাহ ও বন্য পশুর ভয় ছাড়া আর কোনো ভয় জাগ্রত হবে না। [খাব্বাব (রা.) থেকে বোখারী ও মেশকাত]
পশ্চিমা সভ্যতার সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হওয়ার পর আমাদের সমাজের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা হারিয়ে যায়। কঠোর আইন ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ পুলিশও আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। বরং আমাদের সমাজে পুলিশের অবস্থান নানা কারণে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। সরকারি ভাষ্যে পুলিশকে জনগণের বন্ধু বলা হলেও বাস্তবতা বিপরীত। জনগণ পুলিশকে দেখে আতঙ্কিত হয়, এমনকি মায়েরা বাচ্চাদের পুলিশের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়। পুলিশের দুরাচারিতা প্রকাশ করতে বাংলা ভাষায় প্রবচন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, ‘বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।’ অধিকাংশ মানুষের চোখে পুলিশ এখন রক্ষক নয়, ভক্ষক। পুলিশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো লাগামহীন দুর্নীতি, ঘুষ, অন্যায়ভাবে গ্রেফতার, হয়রানি, মুক্তির জন্য অর্থ দাবি এবং রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করা। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, গ্রেফতার, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং দমন-পীড়ন চালাতে পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল নয়, সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালী শ্রেণিও তাদের প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে পুলিশকে পেটোয়া বাহিনীর মতো ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের কার্যকলাপ পুলিশের নৈতিকতা ও পেশাদারিত্বের প্রতি জনগণের আস্থাকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে গেছে। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই পুলিশের চাকরিতে যোগদান করেন কিন্তু পরিস্থিতির তাগিদে বেশিভাগ পুলিশই আর সৎ থাকতে পারেন না, কারণ প্রচলিত মানবরচিত সিস্টেমটাই এমন। পথই যখন বাঁকা হয় তখন গাড়ি সোজা চলতে পারে না।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, দুর্নীতির তালিকায় পুলিশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর নিচু স্তর থেকে শুরু করে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত ঘুষের অর্থ বণ্টনের প্রক্রিয়া চলে, যা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। পুলিশের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনসহ সাধারণ জনগণের প্রতি অমানবিক আচরণ, শারীরিক নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও প্রচুর। এমনকি রাজনৈতিক চাপ ছাড়াও নিছক অর্থের লোভে পুলিশের একটি অংশ সাধারণ নাগরিকদের উপর অত্যাচার চালায়। এছাড়া, বহু পুলিশ সদস্য সন্ত্রাসী, মাদক চোরাকারবারি এবং বিভিন্ন অপরাধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।
পুলিশ বাহিনীর বর্তমান হতাশাজনক পরিস্থিতির পেছনে এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাকালের ইতিহাসের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। আধুনিক পুলিশ বাহিনীর জন্ম হয় ঔপনিবেশিক যুগে। এটি সকলেরই জানা যে, ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকেই বাংলায় শুরু হয় ভয়াবহ অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। নবাবের প্রশাসনের বেতনভুক্ত হাজার হাজার সৈন্য, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজদের ব্যয় বহন করা পরবর্তী পুতুল নবাবদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনিতেই এ সময়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নিরাপত্তাহীনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তার উপরে দ্বৈত শাসনের সময়জুড়ে চাকরিহারা পাইক পেয়াদারা চোর-ডাকাত ধরে তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ ছিনিয়ে নিত, কখনও তারা নিজেরাই চুরি ডাকাতি করত, কখনও তারা তস্করদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লুটের মাল বাটোয়ারা করে নিত।
১৭৯২ সালে প্রথমবার ব্রিটিশরা পুলিশ-ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস Regulations for the Police of the Collectorships in Bengal, Behar and Orissa নামে একটি প্রবিধান প্রণয়ন করেন। সেই প্রবিধানের একাধিক ধারা এখনও বলবৎ আছে। এর মধ্যে ১৫ নম্বর ধারা ছিল- ‘চোরাই বা লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার করার জন্য দারোগাগণ উক্ত সকল মালের মূল্যের ওপর ১০% হারে কমিশন পাবে।’ (কাবেদুল ইসলাম, অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস)। ফলে দেখা গেল, চোর-ডাকাত পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য লুণ্ঠিত মালের মূল্যের ১০ শতাংশের চেয়ে বেশি অর্থ পুলিশকে প্রদান করে পার পেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে যখন ভালো কাজের কেবল আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার রীতি তৈরি করা হলো তখন স্বাভাবিকভাবেই ঘুষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেল।
ভারতে ১৮৬১ সালে Indian Police Act of 1861 প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই হচ্ছে আধুনিক পুলিশ বাহিনীর কাঠামো, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণের মূল ভিত্তি। এই আইনের অধিকাংশ ধারা এখনও চালু আছে, শুধু সময়ের প্রয়োজনে কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। ব্রিটিশ যুগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশের প্রধান কাজ ছিল স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকারীদের উপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালানো। তাই গোড়া থেকেই পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বৈরী এবং আজও পুলিশ জনগণের বন্ধু বলে বিবেচিত নয়।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং বিভাগটিকে কার্যকরভাবে পরিচালিত করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, তা হলো:
১. জনগণের সেবা ও সহযোগিতা: পুলিশ বাহিনী মূলনীতি হতে হবে- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান। কেবল অপরাধীকে পাকড়াও করাই নয়, জনগণের সমস্যাগুলো সমাধান করা, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুঃখ-দুর্দশায় তাদের পাশে দাঁড়ানোও হবে পুলিশের দায়িত্ব। এর মাধ্যমে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা হবে পুলিশ বাহিনীর অন্যতম প্রধান কাজ।
২. রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তি: পুলিশ বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকবে এবং কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থে কাজ করতে পারবে না। যদি মিথ্যা মামলা গ্রহণ করা হয়, বানোয়াট তথ্য এজাহারে যুক্ত করা হয় বা তদন্ত প্রতিবেদনে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রদান করা হয়, তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩. পেশাদারিত্ব: কারো ধর্মীয় আচার আচরণের ক্ষেত্রে পুলিশ কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ধর্মের অনুশাসন কে কতটুকু পালন করবে কি করবে না সে ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন থাকবে। পুলিশ তার পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে কেবল ফৌজদারি অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হয়ে কারো সঙ্গে অপেশাদার আচরণ করবে না।
৪. সন্দেহপ্রসূত হয়রানি: আল্লাহ বলেছেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক সন্দেহ পরিহার করো। কেননা, কিছু সন্দেহ তো পাপ।’ (সুরা হুজরাত ৪৯:১২)। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৫ ও ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্বিচারে গ্রেফতার, আটক ও নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই পুলিশ বাহিনী কেবল সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রেফতার করবে এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো হয়রানি বা রিমান্ডের নামে নির্যাতন করবে না।
৫. নারী পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো: পুলিশ বাহিনীতে নারী সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে নারীদের প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন এবং নির্যাতন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সঠিকভাবে তদন্ত এবং প্রতিকার করা হবে। একইভাবে, নারী পুলিশ সদস্যদের দ্বারা নারী অপরাধীদের তদন্ত করা এবং তাদের সংশোধনের জন্য সহায়তা প্রদান করা যাবে।
৬. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং স্বচ্ছতা: পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। এতে করে পুলিশ বাহিনী তাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে এবং দুর্নীতি বা অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। নির্দিষ্ট সময় পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন চালানো হবে।
৭. নৈতিক চরিত্র ও পেশাগত দক্ষতার প্রশিক্ষণ: পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে আত্মিকভাবে উন্নত ও আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা মেনে চলার মতো চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি বছর আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তারা পেশাগত দিক থেকে আরও উন্নত হতে পারে। এই প্রশিক্ষণে আইন, মানবাধিকার এবং জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পর্কিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে শেখানো হবে। বিশেষ করে, নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে আচরণ সংক্রান্ত আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
[লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট;
যোগাযোগ: ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৭১১৫৭১৫৮১, ০১৭১১২৩০৯৭৫]